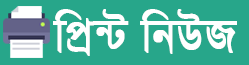প্রথম দুর্গাপূজা-মেধস মুনির আশ্রম! -সোহেল মো. ফখরুদ-দীন

প্রাচীন বাংলার চট্টগ্রামের ইতিহাস অতি সমৃদ্ধ। ইতিহাস গবেষণায় এ প্রাচীন চট্টগ্রামের বয়স সাড়ে চার হাজার বছরেরও বেশি। তার প্রমাণ গবেষণায় সন্ধান পাওয়া যায়। আজ হতে সাড়ে চার হাজার বছর আগে এ জনপদে মানব বসতি ছিল। পাহাড় আর সাগর নদীর পাদদেশে আজকের প্রিয় চট্টগ্রাম। এ চট্টগ্রামের নাম বদল হয়েছে প্রায় ৩৬/৩৭ বার। সবকিছু বদল হয়ে বর্তমানে চট্টগ্রাম ও চিটাগাং নামে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। চট্টগ্রামের ইতিহাসের সাথে ধর্মীয় প্রভাব সবসময় ছিলো জোরালো ভাবে। হিন্দু ধর্মীয় সেই প্রাচীন মহাভারতে চট্টগ্রামের তিনটি মন্দিরের নামের সন্ধান পাওয়া যায়। আদিনাথ, চন্দ্রনাথ ও কাঞ্চননাথের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অন্যদিকে পুরাণে সন্ধান পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রথম সূচনা লগ্নের দুর্গাপূজার স্থান মেধস মুনির আশ্রমের কথা। অপরদিকে রামায়ণ ও কুমারসম্ভেবে বর্ণিত হয় মহেশখালীর দ্বীপ মৈনাক পর্বত আদিনাথ শিবের মন্দিরের কথা। চট্টগ্রামে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ পাহাড়ি অঞ্চলের ুদ্র ুদ্র জাতি গোষ্ঠী বসবাস করে চলেছেন সেই প্রাচীন সময় থেকে। ধর্মীয় চেতনায় এ অঞ্চলের মানুষগুলো পাশাপাশি বসবাস করেন। যার যার ধর্ম, সে মতানুসারে মেনে চলেন। পারস্পরিক বন্ধু ও স্বজনরূপে। ঈদ পুজা পার্বণে একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে চলছেন সেই প্রাচীন কাল থেকেই। বাঙালি হিন্দুদের প্রধান একটি উৎসব দুর্গাপূজা। যা শুরু হয় প্রথম এ চট্টগ্রাম থেকেই। ইতিহাস থেকে জানা যায় তার ইতিকথা।
দুর্গাপূজা এখন আধুনিক পৃথিবীর প্রায় রাষ্ট্রের মধ্যেই পালিত হয়। শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়াসহ এশিয়ার বাকি দেশগুরোতে বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। গর্ব করার বিষয় এখানেই যে, যে পূজা পৃথিবীর সকল দেশে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে সে পূজার প্রাচীন সূচনা এই বাংলাদেশের চট্টগ্রামেই। বাংলাদেশের দণি প্রান্তের প্রাচীন চট্টগ্রামে (প্রাচীন কিরাত অঞ্চল) পাহাড়ি জনপদ বোয়ালখালীর মেধস মুনির আশ্রমে সূচনা হয় আজকের দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সূচনা ও প্রচলন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, “পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজন-প্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলেই এর নাম বাসন্তীপূজাও বলা হয়।”
ইতিহাসবিদ ও ধর্ম গবেষকদের মতে, যে মেধস মুনির আশ্রমের কথা পুরাণে উল্লেখ হয়েছে সে স্থান চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে। যদিও সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গ দেশে প্রথম দুর্গাপূজা রাজশাহী কিংবা ভারতের নদীয়া জেলাতে শুরু হয় মর্মে অনেক গবেষক উল্লেখ করলেও আমরা ঐতিহাসিক পুরাণ গ্রন্থের মতে এটিই প্রমাণিত মেধস মুনির আশ্রমেই প্রথম দুর্গাপূজার সূচনা হয়। আদি প্রাচীন কালেই প্রথম পূজা এই চট্টগ্রামেই মাটিতে সূচনা হয়।
ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক ও সমগ্র পৃথিবীর হিন্দু ধর্মীয় মহাপবিত্র তীর্থভূমি এই মেধস মুনির আশ্রম চট্টগ্রামের বোয়ালখালী করলডেঙ্গা পাহাড়ে। গৌরবময় ইতিহাসের সাী হয়ে আজ দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র পাহাড়, মন্দির ও আশ্রম। রাজ্য হারা রাজা সুরথ স্মৃতিবিজড়িত এই মন্দির মেধস মুনির আশ্রম সংস্কার সংরণ খুবই জরুরী। সরকার উদ্যোগ নিয়ে এটিকে সংস্কার ও আন্তর্জাতিকমানের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে পারলে বহির্বিশ্বে গৌরবের এই পবিত্র ইতিহাস ছড়িতে পড়বে। মেধস মুনির ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসও বিশ্ববাসী জানবে।
দুর্গাপূজার উৎপত্তি স্থান মেধস মুনির আশ্রম প্রসঙ্গে ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র মেধস মুনির আশ্রমকে দেশের সেরা পুরাকৃতি ও জাতীয় আশ্রম ঘোষণার দাবি জানিয়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই লিপিতে বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই সনাতন-ধর্মাবলম্বীরা সাড়ম্বরে উদযাপন করে আসছে দেবী দুর্গার আরাধনা বা শক্তিপূজা। এ শারদীয় দুর্গোৎসব এখন সর্বজনীন উৎসবে পরিগণিত। এ দুর্গাপূজার উৎস ও মর্ত্যলোকে মায়ের আবির্ভাব নিয়ে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। জনশ্র“তি রয়েছে, বোয়ালখালী করলডেঙ্গা পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত মেধস মুনি আশ্রম থেকেই আরাধনা-শক্তি পূজার উৎপত্তি। পৌরাণিকেও তা উল্লেখ রয়েছে। দুর্গাপূজার উৎপত্তিস্থল খ্যাত চণ্ডতীর্থ এ মেধস আশ্রম পড়ে রয়েছে অযতেœ-অবহেলায়। এ আশ্রমকে জাতীয় আশ্রম ঘোষণার দাবি-পরিকল্পনা উপেতি রয়ে গেছে। আশ্রমের ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, বোয়ালখালী উপজেলার করলডেঙ্গা পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত মেধস আশ্রমে মেধস মুনি নামের এক সাধক-ঋষি যোগবলে শত সহস্র বছর আগে দেবী ভগবতির আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন। মেধা মুনির কাছে দেবী মাহাত্ম্য অবগত হয়ে রাজ্যহারা রাজা সুরথ ও স্বজন বিতাড়িত বণিক সমাধি বৈশ্যই সর্বপ্রথম মর্ত্যলোকে শক্তির আরাধনা বা মায়ের পূজা প্রবর্তন করেন। সনাতন-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ পুরাণ, চণ্ডী, দেবীভাগবতে, মার্কেণ্ডয় ও কামাখ্যা পটলে মেধা আশ্রমের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাতে উল্লেখ রয়েছে, ‘ভারতবর্ষের অন্যতম তীর্থস্থান মেধস আশ্রম। মুনি মেধা কোন কালের তা জ্ঞান দৈন্যবশত জানার উপায় নেই। তবে তিনি যে পুরাণোক্ত মুনি তা বিজ্ঞজনদের অজানা নয়। একইভাবে তিনি কোন্ কালে চট্টলভূমির মহাতীর্থ চন্দ্রনাথের দণি-পূর্বাংশের এক গিরিশীর্ষে আশ্রম বা সাধনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কেও আজ জানার উপায় নেই। একালের মানুষের সৌভাগ্য যে, আজ থেকে ১১৫ বছর আগে মেধা মুনির আশ্রমটি বিস্মৃতির অতল থেকে পুনরুদ্ধার বা পুন:আবিষ্কার করা হয়।
বোয়ালখালী উপজেলার আহলা-করলডেঙ্গা ইউনিয়নের করলডেঙ্গা পাহাড় চূড়ায় মেধস মুনির আশ্রম অবস্থিত। প্রায় সমতল থেকে পাঁচশত ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পাহাড়েই এ আশ্রম। পাশের পাহাড় চূড়ায় রয়েছে শিব ও কালি মন্দির। গত পাঁচ বছর আগে স্থাপন করা হয়েছে নান্দনিক শিল্পীশৈলিতে নির্মিত কামাখ্যা মন্দির।
বরিশালের গৈলা অঞ্চলের পন্ডিত জগবন্ধু চক্রবর্তীর ঘরে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ২৫ অগ্রহায়ণে জন্ম নেন চন্দ্রশেখর। জন্মের দুবছর পর মারা যান তাঁর পিতা। মায়ের অনুরোধে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন মাদারীপুরের রাম নারায়ণ পাঠকের কন্যা বিধূমুখীকে। ছয় মাস পর মারা যান স্ত্রী। এর কিছুদিন পর মারা যান মা। সংসারে আপন বলতে আর কেউ রইল না চন্দ্রশেখরের। একাকিত্ব জীবনে এসে চন্দ্রশেখর নানা বেদ শাস্ত্র পাঠ করে হয়ে ওঠেন পরিচিত পণ্ডিত। তখন নাম হল শীতলচন্দ্র। তিনি মাদারীপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃত কলেজসহ নানা শিা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে যোগীপুরুষ স্বামী সত্যানন্দের সাথে সাাতের পর চন্দ্রশেখরের মনে চন্দ্রনাথ দর্শনের তীর্ব আগ্রহ জন্মে। তিনি চলে আসেন সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহায়ে। সেখানে তিনি বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করেন। ততদিনে চন্দ্রশেখর হয়ে ওঠেন বেদানন্দ স্বামী। যোগবলে বেদানন্দ দর্শন লাভ করেন চন্দ্রনাথের (শিব)। চন্দ্রনাথ সেই দর্শনে বেদানন্দকে পাহাড়ের অগ্নিকোণে দৃষ্টি নিবন্ধ করার আদেশ দিয়ে বলেন, ‘দেবীর আবির্ভাবস্থান মেধস আশ্রম পৌরাণিক শত সহস্র বছরের পবিত্র তীর্থভূমি। কালের আবর্তে সেই পীঠস্থান অবলুপ্ত হয়ে পয়েছে। তুমি স্বীয় সাধনাবলে দেবীতীর্থ পুন:আবিষ্কার করে তার উন্নয়নে মনোনিবেশ কর। দেবী দশভূজা দুর্গা তোমার ইচ্ছ পূরণ করবে। দৈববলে প্রভূ চন্দ্রনাথের আদেশে বেদানন্দ স্বামী পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ করে করলডেঙ্গার সন্ন্যাসি পাহাড় চূড়ায় সেই মেধস আশ্রম আবিষ্কার করেন। পরে ভারতবর্ষের পণ্ডিত ও গবেষকেরা এই স্থানকেই প্রাচীন মেধস মুনির আশ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অবাঙালি হিন্দুরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে এ উৎসব পালন করে। যেমন কাশ্মীর ও দাণিাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিংগুলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা এবং কুমারিকা প্রদেশে কন্যাকুমারী নামে দেবীর পূজা ও উৎসব পালিত হয়।
দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর নামে এক দানব স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষমর্দিনী। কালীবিলাসতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুর্গোৎসববিবেক, দুর্গোৎসবতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।
দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম ‘বাসন্তী’ পূজা।
কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্রের শুকপ,ে আর শারদীয়া পূজা হয় সাধারণত আশ্বিনের কখনও বা কার্তিকের শুকপ।ে বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত। এসময় শুকা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নমবী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এদিন দশোহরার মেলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নতুন পোশাক পরে দশোহরার মেলায় যায়।
দুর্গাপূজা তিন প্রকার: সাত্ত্বিক (জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ ভোগ দ্বারা পূজা), তামসিক (কিরাতদের জন্য বিহিত; এতে জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্র নেই; মদ্য, মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূজা করা হয়) ও রাজসিক (পশুবলি ও আমিষ ভোগ দ্বারা পূজা করা হয়)। অতীতে দুর্গাপূজার সময় ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ, শূকর, গন্ডার, ব্যাঘ্র, গোসাপ, কচ্ছপ বা পাখি বলি দেওয়া হতো।
দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি।
প্রতিমার রং হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়গে বা জলে। দুর্গাপূজায় হিন্দুদের সকল বর্ণের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে।
বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩)। কিন্তু জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দুর্গোৎসবনির্ণয়, বিদ্যাপতির (১৩৭৪-১৪৬০) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) দুর্গোৎসববিবেক, কৃত্তিবাস ওঝার (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ, বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) ক্রিয়াচিন্তামণি, রঘুনন্দনের (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণ কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকে কলকাতায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত।
চট্টগ্রামের ইতিহাসের গৌরব কাহিনী নিয়ে আমরা গর্বে পথ চলি। সেই প্রাচীন চট্টগ্রামের বয়স নির্ণয়ে চট্টগ্রামের ৩টি প্রাচীন মন্দিরের নামের ভূমিকা অপরিসীম। কত বছর আগে চট্টগ্রামে মানব বসতি! কেমন ছিল এ অঞ্চলের মানুষ! এর ইতিহাস পাওয়া যায় মহাভারতে। শ্লোক পাঠে ইতিহাসে জানা যায়, প্রাচীন ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকে আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, কাঞ্চননাথ এর কথা উঠে এসেছে। সেই বর্ণনায় আদিনাথ মন্দির মহেশখালীতে, চন্দ্রনাথ মন্দির সীতাকুন্ড, কাঞ্চননাথ মন্দির ফটিকছড়িতে অবস্থিত। বলা হয় ৬ হাজার বছর আগে মহাভারত রচিত হয়। কারো কারো দৃষ্টিতে তারই আগে। আমরা মহাভারতের উল্লেখিত আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, কাঞ্চননাথের সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে বলা যায় এই মাটির পবিত্র তীর্থ তিনটিই। আমরা মহাভারতের পথের অনুসরণে বলতে পারি ৬ হাজার বছর আগেও এ চট্টগ্রামের মানববসতি ছিল। দুর্ভাগ্য যে, ৬ হাজার বছরের প্রাচীন এই তিনটি মন্দির আজও প্রতœ আইনের ইতিহাসে সরকারিভাবে সংস্কার সংরণ কোনটিই হয়নি। হয়নি তেমন কোন উন্নয়নও। অথচ আধুনিক বিশ্বে একশত বছরের প্রাচীন স্থাপনা ও জায়গাকে তারা সংরণ করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। আর আমাদের দেশের ৬ হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির ও পাহাড় ধ্বংস হতে চলেছে। সরকারি উদ্যোগ না পেলে ধ্বংস হয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই হবে এই প্রাচীন মন্দিরের। আসুন আমরা এই প্রাচীন মন্দিরগুলো স্থায়ীরূপে প্রতœ আইনে সংরণ করে দেশ বিদেশে তার ইতিহাস তুলে ধরি।
চন্দ্রনাথ মন্দির: বাংলাদেশের সীতাকুন্ডের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহায়ের উপরে অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির অন্যতম বিখ্যাত শক্তিপীঠ। সীতাকুণ্ড অপরূপ প্রাকৃতিক সৌর্ন্দয্যের লীলাভূমি। এ এলাকাকে হিন্দুদের বড় তীর্থস্থান বলা হয়। এখানের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির। আর অন্যান্য আরো রয়েছে বড়বাজার পূজা মণ্ডপ, ক্রমধেশ্বরী কালী মন্দির, ভোলানন্দ গিরি সেবাশ্রম, কাছারী বাড়ি, শনি ঠাকুর বাড়ি, প্রেমতলা, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রাহ্মচারী সেবাশ্রম, শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গিরিশ ধর্মশালা, দোল চত্বর, এন,জি,সাহা তীর্থযাত্রী নিবাস, তীর্থ গুরু মোহন্ত আস্তানা, বিবেকানন্দ স্মৃতি পঞ্চবটি, জগন্নাথ আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, মহাশ্মশানভবানী মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিগয়াতে, জগন্নাথ মন্দির, বিরুপা মন্দির, পাতালপুরী, অন্নপূর্ণা মন্দির ইত্যাদি। এখানে হিন্দু পবিত্র গ্রন্থসমূহ অনুসারে সতী দেবীর দণি হস্ত পতিত হয়েছিল। সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির তীর্থযাত্রীদের জন্য এক পবিত্র স্থান। এর পুরানো নাম ছিলো “সীতার কুন্ড মন্দির”।
গুরুত্ব: সত্য যুগে দ যজ্ঞের পর সতী মাতা দেহ ত্যাগ করলে মহাদেব সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রলয় নৃত্য শুরু করলে বিষ্ণু দেব সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ ছেদন করেন। এতে সতী মাতার দেহখণ্ডসমূহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং এ সকল স্থানসমূহ শক্তিপীঠ হিসেবে পরিচিতি পায়।
ইতিহাস: রাজমালা অনুসারে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে গৌরের বিখ্যাত আদিসুরের বংশধর রাজা বিশ্বম্ভর সমুদ্রপথে চন্দ্রনাথে পৌঁছার চেষ্টা করেন। ত্রিপুরার শাসক ধন মানিক্য এ মন্দির থেকে শিবের মূর্তি তার রাজ্যে সরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হন।
বিভিন্ন তথ্য অনুসারে এখানের ইতিহাস সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়। প্রাচীন নব্যপ্রস্তর যুগে সীতাকুণ্ডে মানুষের বসবাস শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। এখান থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের আসামিয় জনগোষ্ঠীর হাতিয়ার গুলো তারই স্বার বহন করে। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। এর পরের শতাব্দীতে এই অঞ্চলের শাসনভার চলে যায় পাল সম্রাট ধর্মপাল দ্বারা এর হাতে (৭৭০-৮১০ খ্রী.)। সোনারগাঁও এর সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রী.) ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ অঞ্চল অধিগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুর বংশের শের শাহ্ সুরির নিকট বাংলার সুলতানি বংশের শেষ সুলতান সুলতান গিয়াস উদ্দীন মুহাম্মদ আজম শাহ্ (যার সমাধি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও) পরাজিত হলে হলে এই এলাকা আরাকান রাজ্যের হাতে চলে যায় এবং আরাকানীদের বংশধররা এই অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। পরবর্তীতে পর্তুগীজরাও আরাকানীদের শাসনকাজে ভাগ বসায় এবং ১৫৩৮ খ্রী: থেকে ১৬৬৬ খ্রী: পর্যন্ত এই অঞ্চল পর্তুগীজ ও আরাকানী বংশধররা একসাথে শাসন করে। প্রায় ১২৮ বছরের রাজত্ব শেষে ১৯৬৬ খ্রী. মুঘল সেনাপতি বুজরুগ উন্মে খান আরাকানীদের এবং পর্তুগীজদের হটিয়ে এই অঞ্চল দখল করে নেন।
শিব চতুর্দশী মেলা: এই মন্দিরে প্রতিবছর শিবরাত্রি তথা শিবর্তুদশী তিথিতে বিশেষ পূজা হয়; এই পূজাকে কেন্দ্র করে সীতাকুণ্ডে বিশাল মেলা হয়। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহায় এলাকা বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রতি বছর বাংলা ফাল্গুন মাসে বড় ধরনের একটি মেলার আয়োজন করে থাকে। যেটি শিবর্তুদর্শী মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য সাধু এবং নারী-পুরুষ যোগদান করেন।
আদিনাথ মন্দির: চতুর্দিকে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত মহেশখালী দ্বীপের অন্যতম দর্শনীয় স্থান আদিনাথ মন্দির। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৮৮ ফুট উঁচু মৈনাক পাহাড় চূড়ায় আদিনাথ মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১০.৮৭ মিটার, প্রস্থ ৮.৬২ মিটার, উচ্চতা ৫.৯৩ মিটার। তিনভাগে বিভক্ত প্রথম ভাগে ৩.৩৫ মিটার বর্গাকৃতির দু’টো পূজা ক রয়েছে। পূর্বকে বাণলিঙ্গ শিবমূর্তি আর পশ্চিম কে অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তি। শিবের সাথে মন্দিরে একটি গভীর সম্পর্ক বলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে থাকেন। শিবকে রাবন কাঁধে করে কৈলাস পর্বত থেকে লংকার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে শিব এ মৈনাক পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন বলে তাদের বিশ্বাস। এছাড়া এলাকার প্রচলিত কিংবদন্তি মতে মহেশখালীর প্রভাবশালী জনৈক নুর মোহাম্মদ সিকদারের স্বপ্নের অলৌকিক নির্দেশমতে জানতে পারেন যে, স্বপ্নে দেখা শিলাখণ্ডটি হিন্দুদের ‘দেববিগ্রহ’। এ দেব বিগ্রহের অনেকগুলো নামের মধ্যে ‘মহেশ’ ও ‘আদিনাথ’ নাম দু’টো অন্যতম। দেববিগ্রহের নামানুসারে দ্বীপের নাম মহেশখালী আর মণ্ডপের নাম ‘আদিনাথ মন্দির’ নামকরণ বলে ধারণা করা হয়। সে যাই হোক এ মন্দিরকে ঘিরে প্রতি বছর এখানে শিব চর্তুদশী মেলা আয়োজন করা হয়। শিব ভক্তের প্রভাবে মহেশখালীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান শারদীয় দূর্গোৎসব সাড়ম্বরভাবে উদযাপন করা হয় না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রচুর পূণ্যার্থী ও দর্শণার্থী এ উপলে মহেশখালীতে সমাগম ঘটে থাকে। ছেলেমেয়ে পাওয়ার জন্য কিংবা প্রাপ্ত ছেলেমেয়ের দীর্ঘায়ুর জন্য মানস করে থাকে বলে অনেক নারী-পুরুষকে মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে পশুপাখি বলি দিতে দেখা যায়। এ সময়ে সনাতন ও রাখাইন ঘরে ঘরে আগত অতিথিদের সাধ্যমত আপ্যায়নের নিমিত্ত স্থানীয়রা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আদিনাথ মন্দিরের পাশে বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন প্যাগোডা আছে।
মহেশখালী চ্যানেল সংলগ্ন পশ্চিম পাশে মৈনাক পাহাড়টি অবস্থিত। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে আদিনাথ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। আদিনাথ মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন ২১৭ একর বিশিষ্ট জমি এক সময়ে থাকলে বর্তমানে প্রতিনিয়ত পাহাড় ভাঙ্গনের কারণে মন্দিরের পূর্ব পাশের বিস্তর জমি সমুদ্রের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। এ মন্দিরের পাশেই কক্সবাজার জেলা পরিষদ কর্তৃক আদিনাথ জেটি সম্প্রতি নির্মিত হওয়ায় পর্যটকদের এখানে আগমন আরো সহজতর হয়েছে। আদিনাথ মন্দিরের পাদদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের একটি পাড়া ও ঠাকুরতলা বৌদ্ধ বিহার নামে একটি বিহার রয়েছে।
তথ্যসূত্র: (১) চট্টগ্রামের ইতিহাস-ওহিদুল আলম; (২) ইতিহাস প্রসঙ্গ-সোহেল মো. ফখরুদ-দীন; (৩) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত-অনুবাদ: রাজশেখর বসু; (৪) বাল্মীকি রামায়ণ-অনুবাদ: রাজশেখর বসু; (৫) প্রবন্ধ-ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম; (৬) প্রাচীন চট্টগ্রামের ইতিহাস-সোহেল মো. ফখরুদ-দীন, দৈনিক আজাদী; (৭) কিরাত বাংলার ইতিকথা-সোহেল মো. ফখরুদ-দীন; (৮) মেধস মুনির আশ্রমের ইতিহাস-অরুণ দাশগুপ্ত; (৯) চট্টগ্রামের ইতিহাস-চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদবম্মা; (১০) ইতিহাস এতিহ্য-শতদল বড়–য়া; (১১) আদিনাথ মন্দির প্রসঙ্গে-সোহেল মো. ফখরুদ-দীন; (১২) চন্দ্রনাথ মন্দির ও মেলা পার্বণ-সোহেল মো. ফখরুদ-দীন; (১৩) মেধস আশ্রম-ডা. বরুণ কুমার আচার্য বলাই।
লায়ন মোঃ আবু ছালেহ্ সম্পাদিত ও প্রকাশিত কপিরাইটঃ দৈনিক চট্টগ্রামের খবর ২০২০, সর্বস্বত্ত স্বত্তাধিকার সংরক্ষিত