ভাষা আন্দোলন সূচনাকারী বই: পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা – না উর্দু? ডা. মআআ মুক্তাদীর
- সময় মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ১৮৩ পঠিত

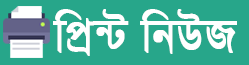
যে গ্রন্থের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যার মধ্যে আন্দোলনের কারণ, যুক্তি এবং আন্দোলন পরিচালনার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল—সেই গ্রন্থকেই যথার্থ অর্থে ভাষা আন্দোলন সূচনাকারী গ্রন্থ বলা যায়। স্বাধীনতার মাত্র এক মাস পরেই, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে জাতিকে সঠিক পথ দেখানোর লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস এমন এক ঐতিহাসিক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করে।তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আবুল কাসেম এই বই প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গ্রন্থটির নাম ছিল— “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা – না উর্দু”। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১০টায় ঢাকার আজিমপুরস্থ ১৯ নম্বর ভবনের ভাষা আন্দোলন অফিসে বইটির আনুষ্ঠানিক পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক আবুল কাসেম স্বয়ং বইটি পাঠ করেন।
সেই সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন— সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ কে এম আহসান, নুরুল হক ভুঁইয়া, শামসুল আলম, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, ফজলুর রহমান ভুঁইয়া, কবি মোফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁদের উপস্থিতি এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে।
গ্রন্থটিতে মোট তিনটি নিবন্ধ স্থান পেয়েছিল,১ . “আমাদের প্রস্তাব” – অধ্যাপক আবুল কাসেম।২. “রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা” – ড. কাজী মোতাহার হোসেন। ৩. “বাংলাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে” – আবুল মনসুর আহমদ। মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার হলেও এই ছোট্ট বইটিই ভাষা আন্দোলনের আদর্শ, যুক্তি ও কর্মপন্থার এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে দাঁড়ায়। এতে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয় কেন বাংলাই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত এবং পূর্ববাংলার জনগণের সাংস্কৃতিক-ভাষাগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য।এই বইটি শুধু ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণাই দেয়নি, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনসহ পরবর্তী সব গণআন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বাস্তবে এ গ্রন্থই জাতিকে প্রথমবারের মতো ভাষা-আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেছিল। ২০২৫ সালে এই অমূল্য প্রকাশনার ৭৮তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। বইটি আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তা জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রাণশক্তি।
লেখক: ভাষা-আন্দোলন স্মৃতি রক্ষা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। ঢাকা, বাংলাদেশ।

রাঙ্গামাটিতে বার্ষিক আনন্দ ভ্রমণ ও মিলন মেলায় মানবাধিকার ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ


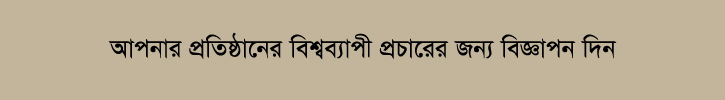



















Leave a Reply